


সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে প্রাকবর্ষা ও বর্ষায় বজ্রপাতের সংখ্যা ও বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে বলে অনেকেই মনে করছেন। আগে দুর্যোগ হিসেবে চিন্তার কারণ ছিল ঝড়-বন্যা। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বজ্রপাত। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৫-২০২০ সালে বাংলাদেশে তিন ধরনের বজ্রপাত সংঘটিত হয়। এক মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে বা আন্তমেঘ, একই মেঘের এক স্থান থেকে আরেক স্থান বা অন্তমেঘ এবং মেঘ থেকে ভূমিতে। এই সময়ে ওই তিন ধরনের বজ্রপাতের মোট পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৫০ লাখ। এগুলোর দৈনিক ও ঋতুভিত্তিক সংঘটনে আবার ভিন্নতা দেখা গেছে। বজ্রপাতের কারণে প্রায়শই মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বেশিরভাগ সময় বিচ্ছিন্নভাবে এক দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। আবার কখনও কখনও একটিমাত্র বজ্রপাতে বহু মানুষ মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে।
বজ্রপাতের কারণে মূলত দুটি উপায়ে মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। একটি কারণ প্রত্যক্ষ বা সরাসরি আঘাত যা মানুষের শরীরের ওপর সরাসরি পড়ে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরোক্ষ আঘাত। সরাসরি আঘাতে মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কম। এধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। বিশ্বব্যাপী যত মানুষের মৃত্যু হয় তার মধ্যে সবচেয়ে কম মৃত্যু হয় প্রত্যক্ষ আঘাতের কারণে। এটি দুর্লভ ঘটনা। বেশিরভাগ মৃত্যুই হয় পরোক্ষ আঘাতের কারণে। পরোক্ষ আঘাতও কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- যেখানে বজ্রপাত আঘাত হানছে সেখানকার পুরো জায়গাটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যাওয়া। একে বলা হয় ভূমির বিদ্যুতায়ন। এভাবেই সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে।
বজ্রপাত ভূপৃষ্ঠের যে স্থানে আঘাত করে সেখান থেকে বিদ্যুৎ ভূমির সকল দিকে চলাচল করতে পারে। মোটামুটি তিন কিলোমিটার এলাকা বিদ্যুতায়িত হতে পরে। কেউ যদি বজ্রপাতের লক্ষ্যের কাছাকাছি থাকে, তবে ভূমির বৈদ্যুতিক প্রবাহে তার মৃত্যু হতে পারে। আর যদি বজ্রপাতের সময় ভূমি আর্দ্র থাকে এবং সেখানে যারা থাকবে তাদের মৃত্যু-ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। বজ্রপাতের সময় কেউ যদি কোনো গাছের নিচে থাকে, তখন বজ্রপাত ওই গাছে আঘাত করে এবং বিদ্যুতের কিছু অংশ তার শরীরে পরিবাহিত হয়েও মৃত্যু হতে পারে। বজ্রপাত আঘাত করার পরেও কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে কি না সেটা নির্ভর করে বজ্রপাতের সময় ওই ব্যক্তি কোথায় ছিলেন তার ওপর।বজ্রপাতের লক্ষ্য থেকে তিনি কতোটা দূরে ছিলেন, শরীরের কতোটা অংশ পুড়ে গেছে- এরকম অনেক কিছুর ওপরেই এটি নির্ভর করে।সাধারণত পানির ওপরে থাকলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী।
বজ্রপাতের আঘাতে মানুষের শরীর পুড়ে যায়। তার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। শকওয়েভ সাউন্ড বা প্রচণ্ড শব্দের কারণে মানুষ পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে। নার্ভ সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও আরো নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা, স্মৃতি-ভ্রম ইত্যাদি। সারাবিশ্বেই বজ্রপাতের আঘাতের পরেও বহু মানুষের বেঁচে যাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেউ বৈদ্যুতিক শক পেলে যেমন তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়, সেরকম চিকিৎসা সাথে সাথে দেওয়া গেলে বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকেও বাঁচানো সম্ভব।
বজ্রপাতে বাংলাদেশে ঠিক কতো মানুষের মৃত্যু হয় তার সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্য থেকে ধারণা করা যায় এই সংখ্যা কম বেশি দুশোর উপরে। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে গড়ে ৩০০ মানুষ মারা যায়। দেশের বজ্রপাত পরিস্থিতি এবং হতাহতের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি সংগঠন ডিজাস্টার ফোরাম। প্রতিষ্ঠানটির হিসেবে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ৩ হাজার ৮৭০ জনের, অর্থাৎ প্রতিবছর ২৭৬ জনের বেশি। সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে ২০২১ সালে– ৩৮১ জন। চলতি বছর এপ্রিল মাসের শেষ অব্দি অন্তত ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
বজ্রপাত একটি আকস্মিক ঘটনা এবং পুরোপুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ দুর্যোগ প্রতিহতের উপায় নেই। বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যা বিশ্বে বাংলাদেশেই বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে।আমাদের দেশে বজ্রপাতের শিকার মানুষের বড়ো অংশ কৃষক, যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দিতে মাঠে যান। আর সেখানেই মরে পড়ে থাকেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা সব সময়ই বলে আসছে ঝড়-বৃষ্টিতে ঘরে থাকার বিকল্প নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ডিজাস্টার ফোরামের তথ্য বলছে, সারাবিশ্বে বজ্রপাতে যে সংখ্যায় মানুষ মারা যায়, তার এক-চতুর্থাংশই বাংলাদেশে। দেশের হাওর, বাঁওড় ও বিলপ্রবণ জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশই মাঠে থাকা কৃষক, সাড়ে ১৪ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে আর ১৩ শতাংশ গোসল কিংবা মাছ শিকারের সময়। শহরের ভবনগুলোতে বজ্রপাত প্রতিরোধক দণ্ড থাকায় হতাহতের সংখ্যা কম।
বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে সরকারি নানা উদ্যোগ আছে। একে দুর্যোগও ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরও মৃত্যু কমছে না। ভুল প্রকল্প, বড় গাছ কাটা বন্ধ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরির চেষ্টা না থাকায় মৃত্যু রোধ হচ্ছে না। বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবহাওয়াবিদরা বলছেন, নদী শুকিয়ে যাওয়া, বায়ুদূষণ, জলাভূমি ভরাট হওয়া আর গাছ ধ্বংস হওয়ায় দেশে তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্র বায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে আসা শুষ্ক বায়ুর মিলনে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও মে মাসজুড়ে বজ্রপাত ও কালবৈশাখীর পূর্বাভাস আছে।
প্রতিবছর মার্চ থেকেই শুরু হয় বজ্রপাত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বজ্রপাতে প্রাণহানি কমাতে জনসচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে করণীয় বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বজ্রপাত থেকে রক্ষার বিভিন্ন উপায় আরও বেশি করে প্রচারের পরামর্শও দিয়েছেন তারা। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। নির্দেশনাগুলো হলো বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না। প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যেতে হবে। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাইকে এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করতে। খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসা দিতে হবে।
এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালা বা বারান্দা থেকে দূরে সরে যেতে হবে এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হওয়া যেতে পারে। উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকা যাবে না। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেরাও বিরত থাকতে হবে।
বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়তে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে।বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে। কৃষিকাজ বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতে হবে বা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।
প্রাকৃতিক উপায়ে বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য বেশি করে তালগাছ রোপণ করতে হবে। তালগাছ বজ্রপাত নিরোধক। যেসব তালগাছ বড়ো হয়েছে, সেগুলো কাটা যাবে না; যত্ন করতে হবে। তালের বীজ থেকে চারা গাছ হওয়ার পর সেগুলো বড়ো হওয়ার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।
বজ্রপাত যেমন প্রকৃতির এক অপরিহার্য বাস্তবতা, তেমনি মানুষের জীবন ও জীবিকায় এর প্রভাবও ভয়াবহ। প্রতি বছর শত শত প্রাণহানি আর অসংখ্য পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। অথচ কিছু সচেতনতা ও সতর্কতাই হতে পারে জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। সরকারি উদ্যোগ, জনসচেতনতা, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার মিলেই বজ্রপাতজনিত প্রাণহানি কমানো সম্ভব। এই ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক ভাবনা, নীতিগত পরিকল্পনা ও প্রতিটি মানুষের দায়িত্বশীল আচরণ। প্রকৃতির রুদ্ররূপকে রোধ করা না গেলেও, তা থেকে নিরাপদে বেঁচে থাকার পথ তৈরি করাই হোক আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার।
সেলিনা আক্তার
পিআইডি ফিচার











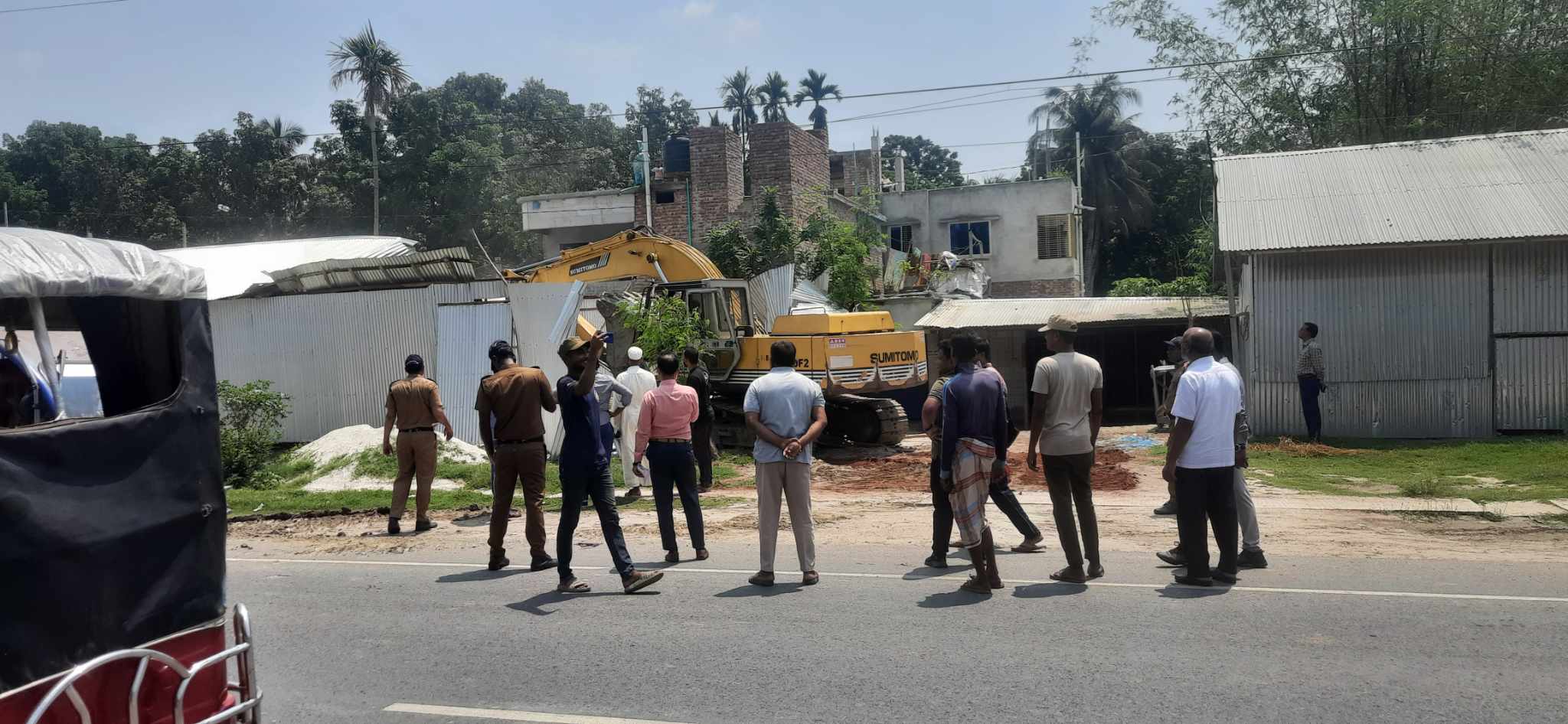










আপনার মতামত লিখুন :